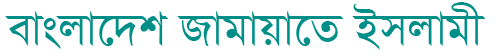জুলাই ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্বের পরিধি এবং তারা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব কত দিনের মধ্যে সম্পাদন করতে পারবেন, তা নিয়ে আলোচনা চলছে। এ ব্যাপারে নাগরিক সমাজের মতো রাজনৈতিক দলগুলোরও সক্রিয় চিন্তা আছে। ফ্যাসিবাদ-উত্তর রাষ্ট্রকাঠামো সংস্কারের কথাও ব্যাপকভাবে জনচাহিদার মধ্যে চলে এসেছে। স্বাভাবিকভাবেই সংবিধান পুনর্লিখন বা সংশোধনের প্রসঙ্গ এসে যায়।
বলাবাহুল্য, দেশের সংবিধান নিয়ে সূচনাতেই বিতর্কের শুরু এবং আজো তা অব্যাহত। তাই সংবিধান নিয়ে ধারাবাহিক কিছু ভাবনা ও ঐতিহাসিক তথ্য তুলে ধরব।
১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর সরকারের প্রথম দায়িত্ব ছিল সংবিধান প্রণয়ন । স্বাধীনতার স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে তৎকালীন সরকার স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সংবিধান প্রণয়ন করে। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল গঠিত মুজিবনগর সরকার কর্তৃক জারি করা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে রাষ্ট্রপতিকে সর্বময় ক্ষমতা দেয়া হয়। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি শেখ মুজিব পাকিস্তান থেকে দেশে ফিরে আসেন। রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিব ১১ জানুয়ারি ১৯৭২ বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন। এতে সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থার কথা বলা হয়। রাষ্ট্রপতি আনুষ্ঠানিক প্রধান হন। ১২ জানুয়ারি ১৯৭২ শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন।
সংবিধান প্রণয়নের পটভূমি
বাংলাদেশের সংবিধান রচনার প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ জারি করা গণপরিষদ আদেশ। সেটি ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে কার্যকর ধরা হয়। এ আদেশ অনুযায়ী ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সালের ১ মার্চ পর্যন্ত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের আসনগুলোয় বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত সব প্রতিনিধিকে নিয়ে গণপরিষদ গঠন করা হয়। গণপরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল ৪৩০ জন। তখন কেউ কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন যে, পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নিয়ে গণপরিষদ গঠন যুক্তিসঙ্গত নয়; কারণ তারা অবিভক্ত পাকিস্তানের সংবিধান রচনার জন্য জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান তৈরির কোনো ম্যান্ডেট তাদের ছিল না। যাই হোক, গণপরিষদ শুধু সংবিধান রচনার অধিকার পায়। অন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা তাদের ছিল না। ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ১৯৭২ সালের ১১ এপ্রিল খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়। এতে ৩৪ জন সদস্য (৩৩ আ’লীগ+১ সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত) ছিল। কমিটি ৭৪টি বৈঠকে বসে এবং ছয় মাসের মধ্যে কমিটি কাজ শেষ করে। কমিটি বিভিন্ন মহল থেকে ৯৮টি সুপারিশ পায়। কমিটির আহ্বানে তেমন সাড়া ছিল না। কারণ কোনো প্রশ্নমালা ছিল না। বিরোধী দলগুলোও উৎসাহী ছিল না। সংবিধানের বাংলা পাঠ প্রণয়নে কমিটিকে সাহায্য করেন সৈয়দ আলী আহসান, ড. মাজহারুল ইসলাম ও ড. আনিসুজ্জামান। একজন ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞ সংবিধান প্রণয়নে সাহায্য করেন। ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর খসড়া সংবিধান বিল গণপরিষদে পেশ করা হয়।
সংবিধান প্রণয়নে বিতর্ক
সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়া নিয়ে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও তার দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি ও বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন যুক্তি উপস্থাপন করে যে, গণপরিষদের সংবিধান প্রণয়নের কোনো বৈধতা নেই। কারণ গণপরিষদ সদস্যদের স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের কোনো ম্যান্ডেট জনগণ দেয়নি; বরং তারা ইয়াহিয়া খানের দেয়া শর্তানুযায়ী ‘লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার’-এর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের ব্যাপারে জনগণের ম্যান্ডেট পেয়েছিল। এমনকি আওয়ামী লীগের নির্বাচনী মেনিফেস্টো বা তাদের নির্বাচনী বক্তৃতায় কোথাও স্বাধীন বাংলাদেশের কোনো ধারণা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জনগণকে দেয়া হয়নি। সুতরাং পাকিস্তানের জন্য নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্যরা স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান তৈরির কোনো অধিকার রাখেন না। তারা দাবি করেন, সংবিধান প্রণয়ন ও গণভোটে তা অনুমোদিত হতে হবে। তাদের দাবি ছিল, সমাজতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে। এ সময় মওলানা ভাসানী ছয়টি দলের সমন্বয়ে ‘সর্বদলীয় অ্যাকশন কমিটি’ গঠন করেন। সংবিধান প্রণীত হওয়ার পর ভাসানী বলেন, ‘একটি বাজে গণপরিষদ কর্তৃক জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়া সংবিধান বাতিল করে সরকারের ভেতরের ও বাইরের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে নতুন খসড়া সংবিধান তৈরির জন্য সরকারের উদ্যোগ নেয়া উচিত। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) ও কৃষক-শ্রমিক সমাজবাদী দল অভিমত প্রকাশ করে, এ সংবিধানে জাতির আশা-আকাক্সক্ষা প্রতিফলিত হয়নি। বিশেষ করে সমাজতন্ত্রের অভিপ্রায় কাগুজে বুলি ছাড়া আর কিছু নয়। এ সময় সোভিয়েতপন্থী ন্যাপ নেতারা, কমিউনিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশ (সিপিবি) ও ছাত্র ইউনিয়ন মৃদু সমালোচনা করে আক্ষেপ প্রকাশ করে, এ গণপরিষদের কাছে পূর্ণাঙ্গ সমাজতান্ত্রিক সংবিধান আশা করা যায় না। আওয়ামী লীগ দাবি করে, প্রণীত সংবিধান একটি উত্তম সংবিধান এবং গণপরিষদও বৈধ।
বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মধ্য থেকে স্বল্পসংখ্যকই সাংবিধানিক বিতর্কে অংশ নেন। রাজনৈতিক দলের মধ্যে মুসলিম জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী দলগুলোর অনুপস্থিতির ফলে সংবিধান সম্পর্কে তাদের কোনো অভিমত প্রকাশিত হয়নি। খসড়া সাংবিধানের ওপর জনমত গ্রহণ বা যাচাইয়ের তেমন কোনো সময় ও সুযোগ দেয়া হয়নি। সংবিধান প্রণয়ন কমিটি সংবিধানের ওপর পরামর্শ আহ্বান করেছিল। কিন্তু জনগণ তাতে তেমন সাড়া দেয়নি। কমিটি জনমত যাচাইয়ের জন্য কোনো প্রশ্নমালা জারি করেনি এবং সময়ও দিয়েছিল মাত্র তিন সপ্তাহ। আবার গণপরিষদে আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যদেরও সংবিধানের ওপর আলোচনার তেমন সুযোগ দেয়া হয়নি। মোট ৪০৪ জন সদস্যের মধ্যে ১৭৫ জন আলোচনার জন্য নাম দিয়েছিলেন। এর মধ্যে মাত্র ৪৮ জনকে সুযোগ দেয়া হয়। এদের এক-তৃতীয়াংশই ছিলেন সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য। আবার ৪৫ জনই আওয়ামী লীগের।
রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি নির্ধারণের নেপথ্যে
১৯৭২ সালের সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়, ‘আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল- জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।’ মূলনীতিগুলো সংবিধানের ৮, ৯, ১০, ১১ ও ১১ অনুচ্ছেদে
নিম্নলিখিতভাবে বর্ণিত হয়েছে :
জাতীয়তাবাদ : সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৯-এ বলা হয়েছে, ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সঙ্কল্পবদ্ধ সংগ্রাম করে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে, সেই বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি হবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।
সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি : সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১০-এ বলা হয়েছে, মানুষের ওপর মানুষের শোষণ থেকে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজ লাভ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে।
গণতন্ত্র ও মানবাধিকার : সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১১-তে বলা হয়েছে, প্রজাতন্ত্র হবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হবে এবং প্রশাসনের সব পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে।
ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা : সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২-তে বলা হয়েছে, ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য- ক. সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা; খ. রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান; গ. রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার; ঘ. কোনো বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তার ওপর নিপীড়ন বিলোপ করা হবে।
এ ছাড়াও সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩ থেকে অনুচ্ছেদ ২৫ পর্যন্ত আরো বেশ কিছু রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি উল্লেখ করা হয়ছে। এর মধ্যে রয়েছে মালিকানা-ব্যবস্থা, কৃষক ও শ্রমিকের শোষণ থেকে মুক্তি, মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা, গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা, সুযোগের সম অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম, নাগরিক ও সরকারি কর্মচারীদের কর্তব্য, নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ, জাতীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা, জাতীয় স্মৃতিনিদর্শন প্রভৃতির সংরক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও শ্রদ্ধা। সংবিধানের অনুচ্ছেদ-২৫-তে বলা হয়েছে, জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসঙ্ঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা- এসব নীতি হবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি এবং এসব নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র- ক. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তিপ্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টা করবে; খ. প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিপ্রায় অনুযায়ী পথ ও পন্থার মাধ্যমে অবাধে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনের অধিকার সমর্থন করবে এবং গ. সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করবে। হ
বাকি অংশ আগামীকাল
সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি নির্ধারণের নেপথ্যে
১৯৭২ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে প্রণীত সংবিধানে যে বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র প্রতিফলিত হয়েছে তা তাদের দলীয় নীতি ও কৌশলের বহিঃপ্রকাশ ছিল। আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিব যেভাবে চেয়েছিলেন, ঠিক সেভাবে সংবিধান তৈরি হয়েছিল। অবশ্য মুজিবের চিন্তাধারায় যেসব অসঙ্গতি ছিল তার প্রভাব সংবিধানেও পড়ে। আওয়ামী লীগের সূচনা থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত তাদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে তাদের নীতি বিচ্যুতিগুলো সহজে ধরা পড়বে।
আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিব কি তাহলে তাদের জীবনাচারের সাথে স্ববিরোধী ধর্মনিরপেক্ষতা নীতিকে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন? বিষয়টি একটু খতিয়ে দেখা যাক। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়। দলটির প্রতিষ্ঠাকালীন সম্মেলনে প্রথম সাধারণ সম্পদক সামসুল হক ‘মূল দাবি’ শীর্ষক একটি পুস্তিকা পাঠ করেন। এতে বলা হয় : ‘পাকিস্তান খেলাফত অথবা ইউনিয়ন অব পাকিস্তান রিপাবলিক ব্রিটিশ কমনওয়েলথের বাইরে একটি সার্বভৌম ইসলামী রাষ্ট্র হবে। ... রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব আল্লøাহর প্রতিভূ হিসেবে জনগণের ওপর ন্যস্ত থাকবে। গঠনতন্ত্র হবে নীতিতে ইসলামী, গণতান্ত্রিক ও আকারে রিপাবলিকান।’ (বদরুদ্দীন ওমর, ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, পৃষ্ঠা-২৪১) দলটির ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্রের ১ নং ধারায় দুনিয়ার মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন শক্তিশালী করতে হবে। ১০ নং ধারায় বলা হয়- To disseminate true knowledge of Islam and its high morals and religious principles among people.. এরপর ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচির অন্যতম দফা ছিল : ‘কুরআন-সুন্নাহর মৌলিক নীতির খেলাফ কোনো আইন প্রণয়ন করা হইবে না এবং ইসলামী সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবনধারণের ব্যবস্থা করা হইবে।’ (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৭০)
১৯৫৫ সালে যখন ‘আওয়ামী মুসলিম লীগ’ নাম পরিবর্তন করে ‘আওয়ামী লীগ’ করা হয়, ওই বছর মে মাসে প্রচারিত এক সাংগঠনিক প্রচারপত্রে দাবি করা হয়, ‘মুসলমানগণ যাতে নামাজ রোজা হজ জাকাত ইত্যাদি শরিয়তসম্মত কাজে অবহেলা না করেন এবং সব শ্রেণীর নাগরিকদের চরিত্র গঠনের জন্য প্রচার (তাবলিগ) বিভাগ খুলিতে হইবে। হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।’
১৯৬৬ সালে ঐতিহাসিক ছয় দফা পেশ করা হয়। এর তার কোনো দফায় ‘সেক্যুলারিজম’ বা ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ সম্পর্কে কোনো কথা বলা হয়নি। ১৯৬৯ সালে স্বৈরাচারী আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে ছাত্র-গণ আন্দোলনে ছাত্রসমাজের যে ১১ দফা পেশ করা হয়েছিল তাতেও ধর্মনিরপেক্ষতার কথা উল্লেখ ছিল না।
১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ঘোষণা করে, ‘কুরআন-সুন্নাহবিরোধী কোনো আইন পাস করা হবে না।’ নির্বাচনে বিজয়ের পর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে রেসকোর্স ময়দানে লাখো মানুষের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ১৬৭ জন এবং প্রাদেশিক পরিষদের ২৮৮ জন মোট ৪৫৫ জন নির্বাচিত সদস্য উপস্থিত ছিলেন। শেখ মুজিব তাদের ‘করুণাময় ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার’ নামে শপথবাক্য পাঠ করান এবং তার সর্বশেষ বাক্যটি ছিল ‘আল্লøাহ আমাদের প্রচেষ্টায় সহায় হোন’।
পাকিস্তান আওয়ামী লীগ তাদের ৬ জুন ১৯৭০-এ কাউন্সিল অধিবেশনে ঘোষণা করে, কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশের বিরুদ্ধে পাকিস্তানে যাতে কোনো আইন পাস হতে না পারে, তজ্জন্য আওয়ামী লীগ শাসনতান্ত্রিক বিধান রাখবে। এতে আরো বলা হয়, শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের পবিত্রতা রক্ষার গ্যারান্টি দেয়া হবে এবং সব পর্যায়ে ধর্মীয় শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হরা হবে। আইনের দৃষ্টিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম-মর্যাদার অধিকারী বিবেচিত হবে এবং আইনের দ্বারা সমানভাবে তাদের নিরাপত্তা বিধান করা হবে। সংখ্যালঘুদের নিজ নিজ ধর্ম আচরণ, প্রচার ও ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। (মওদুদ আহমেদ, বাংলাদেশ শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল, ২০১৬)
১৯৭০ সালে নির্বাচনে বিজয়ের পর আওয়ামী লীগের সংবিধান প্রণয়ন কমিটি পাকিস্তানের জন্য যে খসড়া সংবিধান তৈরি করে তাতে উল্লেখ ছিল, ‘পাকিস্তানের মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে গড়ে তোলা হবে।’ ওই খসড়া সংবিধানে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে বলা হয়েছিল- ১. কুরআন-সুন্নাহবিরোধী কোনো আইন পাস করা হবে না; ২. মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী নৈতিকতা উন্নয়নের পদক্ষেপ নেয়া হবে। অবশ্য ওই খসড়ায় পাকিস্তানে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করার কথা বলা হয়- “With a view to achiving a just and egalitarian society, free from exploitation of man by man, and of region by region, a socialistic economic system shall be established.” (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২, তৃতীয় খণ্ড)
১৯৭১ সালের ৭ মার্চে শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ভাষণে ‘সেক্যুলারিজম’ বা ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’র কোনো কথা বলেননি। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় ‘সেক্যুলারিজম’ বা ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’র কোনো কথা বলা হয়নি; বরং তাতে মুক্তিযুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছিল- ‘বাংলাদেশের জনগণ (১৯৭০-এর নির্বাচনে) নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতি যেই ম্যান্ডেট প্রদান করিয়াছে সেই ম্যান্ডেট অনুযায়ী আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আমাদের সমন্বয়ে গণপরিষদ গঠন করিয়া পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জন্য ‘সাম্য’, ‘মানবিক মর্যাদা’ ও ‘সামাজিক ন্যায়বিচার’ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এ রূপান্তরিত করার ঘোষণা প্রদান করিতেছি।” (প্রাগুক্ত)
১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল প্রবাসী সরকার গঠিত হয়। ১১ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ জনগণের উদ্দেশে যে বেতার ভাষণ দেন তাতে বলেন- ‘বাংলাদেশের নিরন্ন দুঃখী মানুষের জন্য রচিত হোক এক নতুন পৃথিবী যেখানে মানুষ মানুষকে শোষণ করবে না। আমাদের প্রতিজ্ঞা হোক ক্ষুধা, রোগ, বেকারত্ব আর অজ্ঞানতার অভিশাপ থেকে মুক্তি। গড়ে উঠুক নতুন গণশক্তিকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থা, গণমানুষের কল্যাণে সাম্য আর সুবিচারের ভিত্তিপ্রস্তরে লেখা হোক জয় বাংলা, জয় স্বাধীন বাংলাদেশ।’ (প্রাগুক্ত)
১৯৭১ সালের ২৪ এপ্রিল প্রবাসী সরকারের পক্ষ থেকে ভারত সরকারকে চিঠি দেয়া হয় বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য। ওই চিঠিতে স্বাধীনতা ঘোষণা, সরকার গঠন ইত্যাদির কথা উল্লেখ থাকলেও কোনো রাষ্ট্রীয় মূলনীতির কথা ছিল না। ভারত এতে কোনো সাড়া দেয়নি। ১৯৭১ সালের ১৫ অক্টোবর আবার চিঠি দেয়া হয়। সে চিঠিতে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্র্তৃক বিশেষভাবে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর জুলুম-নির্যাতনের ঘটনা উল্লেখ করা হয় যাতে ভারতকে প্রভাবিত করা যায়। ভারত দ্বিতীয় চিঠিরও জবাব দেয়নি। এরপর কোনো এক অদৃশ্য হাতের ইশারায় প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১ সালের ২৩ নভেম্বর প্রথমবারের মতো ভিন্নতর রাষ্ট্রীয় মূলনীতির কথা উল্লেখ করে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য ভারত সরকারকে চিঠি দিয়ে আবেদন জানায়। এ চিঠিতে ভারত স্বীকৃতি না দেয়ায় হতাশা প্রকাশ করে আশ^াস দেয়া হয় যে, ভারত সরকারের নীতির সাথে নতুন বাংলাদেশের বিশেষ কোনো পার্থক্য হবে না। এতে বলা হয়- You have shown unflinching support to the principles of democracy, secularism, socialism and a non-aligned foreign policy…. We should like to reiterate here what we have already proclaimed as the basic principles of our state policy, i.e. democracy, socialism, secularism, and the establishment of an egalitarian society. Where there would be no discrimation on the basis of race, religion, sex, or creed. In our foreign relations, we are determined to follow a policy of non-allignment, peaceful co-existence and opposition to colonialism, racialism and imperialism in all its forms and manifestations. Against this background of this community of ideals and principles, we are unable to understand why the Government of India has not yet responded to our plea for recognition. (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮৯২)
এর পরিপ্রেক্ষিতে ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ ভারতের লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করেন, ‘আমাদেরই মতো গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদের আদর্শে বিশ^াসী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি জানানোর ঘোষণা করছি।’ সেদিন পার্লামেন্টে ‘জয় বাংলা’ স্লেøাগানও দেয়া হয়। (উপেন তরফদার, বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ, জুন ২০০০, ঢাকা)
১৯৭১ সালের ১৮ নভেম্বর আওয়ামী লীগ কলকাতার সল্ট লেকে শরণার্থী শিবিরে এক জনসভার আয়োজন করে। সেখানে তৎকালীন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মীজানুর রহমান চৌধুরী বলেন, ‘বিশে^ একটি মাত্র দেশ ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র আছে তা হলো ভারত। আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টোও তাই। আমরা ইতোমধ্যেই মুক্ত এলাকায় ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সমাজবাদ কায়েমের কাজ শুরু করে দিয়েছি।’ (কলকাতা থেকে প্রকাশিত ‘জয় বাংলা’ পত্রিকা, ১৯ নভেম্বর, ১৯৭১)
প্রবাসী সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম তখন এক প্রচারপত্রে বলেন, অসাম্প্রদায়িকতা বা সেক্যুলারিজমের মহান আদর্শ বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আমরা বিশে^র কাছে তুলে ধরেছি। এই একটি বিষয়ে আপনাদের স্পষ্ট থাকতে হবে। কোনো প্রকারে সাম্প্রদায়িকতার মালিন্য যেন আওয়ামী লীগের সদস্যদের নাম কলঙ্কিত না হয়, সে বিষয়ে আপনাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। গণতন্ত্র অর্থই হলো অসাম্প্রদায়িকতা। যেখানে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি সেখানে গণতন্ত্র কোনোদিন কার্যকর হতে পারে না। আজ আমরা গণতন্ত্রে বিশ^াস করি বলেই অসাম্প্রদায়িকতা বা সেক্যুলারিজমে বিশ^াস করতে হবে। (পিনাকি ভট্টাচার্য, মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম)
শেখ মুজিবুর রহমান ১০ এপ্রিল ১৯৭২-এ পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে ফেরার পথে দিল্লিতে যাত্রাবিরতি করেন এবং সেখানে ইন্দিরা গান্ধীর সাথে এক জনসভায় ভাষণ দেন। সেখানে তিনি বলেন, ‘আমি বিশ^াস করি সেক্যুলারিজমে- আমি বিশ^াস করি গণতন্ত্রে- আমি বিশ^াস করি সোশ্যালিজমে। আমাকে প্রশ্ন করা হয়- ইন্দিরা গান্ধীর সাথে আপনার আদর্শে এত মিল কেন? আমি বলি- এটি আদর্শের মিল- এটি নীতির মিল- এটি মনুষ্যত্বের মিল- এটি বিশ^ শান্তির মিল।’ (উপেন তরফদার, বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ, জুন ২০০০, ঢাকা)
উল্লিখিত ঐতিহাসিক তথ্যগুলো থেকে প্রতীয়মান হয়, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতি স্বীকৃতি আদায় এবং ভারতকে খুশি করার জন্য তাজউদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদকে গ্রহণ করে। কিন্তু সংবিধান যেহেতু একটি রাষ্ট্রের জনগণের একটি সামাজিক চুক্তির বহিঃপ্রকাশ, সেহেতু তার প্রতি জনগণের মতামত গ্রহণের বাধ্যবাধকতা ছিল। কিন্তু চারটি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বিষয়ে আওয়ামী লীগ জনগণকে কখনো জানায়নি এবং এ বিষয়ে কোনো দিন তারা জনগণের কোনো ম্যান্ডেটও পায়নি। এমনকি ১৯৭২ সালের সংবিধান প্রণয়ন করার পরও গণভোটের আয়োজন করা হয়নি। এটি ছিল ওই সংবিধানের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। বস্তুত, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি- গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ ছিল ভারতকে খুশি করার জন্য বাংলাদেশের জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়া একটি অপপ্রয়াস। এ কথারই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব আবুল ফাতেহের কথায়। তিনি বলেন, Secularism came by compulsion because mujibnagar Government (the Provisional Government) was in India and heavily dependent on India for moral, material and diplomatic support. (পিনাকি ভট্টাচার্য, মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম)
লেখক : গবেষক ও বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব